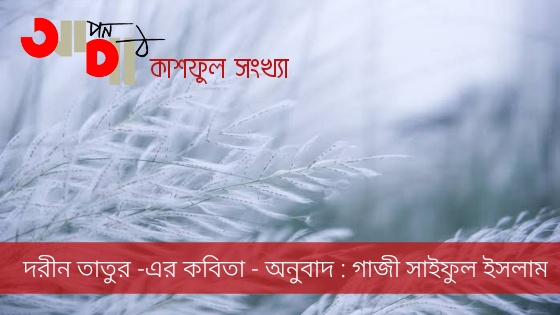যে জগতে দুষ্মন্ত ও ভীম নেই – পি ভাটশালা অনুবাদ: বিপ্লব বিশ্বাস
(মালায়লাম গল্প থেকে অনূদিত)
[লেখক পরিচিতি: পি ভাটশালার (১৯৩৮ -) জন্ম কালিকটে। সরকারি ট্রেনিং স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন। যদিও তাঁর বেশির ভাগ গল্পের মূল চরিত্র মহিলা তবুও তাঁর লেখার ক্ষেত্র বিচিত্র ও বিস্তৃত। তাঁর উপন্যাস Nizhalurangunna Vazhikal (Pathways Where Shadows Sleep)-এর জন্য তিনি কেরালা সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পান। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই হল Nellu (Paddy), Agneyam (Of Fire), Trishnayude Pookkal ( Flowers of Desire)ইত্যাদি। তাঁর বহু লেখায় উত্তর কেরালার ওয়ায়ানাডুর আদিবাসী জীবন উঠে এসেছে। বর্তমান অনূদিত গল্পটি স্বকামী প্রেমের এক খোলামেলা প্রকাশ।]
দীর্ঘকাল আগে যে পুরোনো শহরে ক্লান্তির পথ হেঁটেছি তাকে চিনতে খুব বেশি সময় লাগল না। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে গাড়ির ভিতর কিছুক্ষণ বসে গভীর মনোযোগে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।
সকাল ছটায় বেরিয়েছিলাম আর এখন সাড়ে নটা। মাধবেত্তানকে বাসে আনা ঠিক হবে না বুঝে ট্যাক্সি ভাড়া করেছিলাম। গ্রামের লোকজনও সেটাই চেয়েছিল। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জনাকয় সহৃদয় পড়শি আর পরিচিতজন আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। মাধবেত্তানকে ডাক্তার দেখানো তাদের প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে বলেই যে তারা জড়ো হয়েছিল, তা বলা আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতাই হবে। আমার মতো একা মেয়েলোকের পক্ষে কি তার মানসিকভাবে অসুস্থ স্বামীকে শহরে নিয়ে আসা সম্ভব!
মাধবেত্তানকে দেখানো হয়ে গেলে তারা চলে গেল। বলে গেল, ‘চিন্তা করার কিছু নেই।’
না, আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইনি কেন-না অনেক আগেই বুঝেছিলাম—ঠিক যেদিন সে আমার গলাবেড়ে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দিয়েছিল, যে আমার স্বামী এক অসুস্থ পুরুষ। আমার বয়স তখন ষোলো এবং কাউকেই সে কথা বলতে পারিনি, বললে বিশ্বাসও করত না।
অবশ্য ছোটো ভাইকে বলতে পারতাম। কিন্তু তা কোনও কাজে আসত না। সে তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র আর এ কথা শুনে উপহাসই করত।
আজ যখন ট্যাক্সিতে উঠলাম তার সেই উপহাসের চোখ শুকিয়ে কাঠ।
‘দিদি, তুমি কি হাসপাতালেই থাকবে?’
‘হ্যাঁ।’
সে চুপ মেরে গেল। চলন্ত ট্যাক্সির পেছনের জানলা দিয়ে উঁকি মারলাম। সে বাবার চা-দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল; হাত উলটিয়ে চোখ মুছে সেই জল পাজামায় ঘষছিল।
এখন আমি সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি যা পাঁচ বছর আমার দখলে ছিল। এখন এ জায়গাকে শহর বলা যায় না। এটি এখন নগর, রাজ্যের বড়ো নগরগুলোর একটি, খবরকাগজের পরিসংখ্যান যা বলে।
কিন্তু মায়ের সন্তান যতই বড়ো হোক সে মায়েরই থাকে। আমার মতো যার কোনও সন্তান নেই, এই জায়গাই তার সন্তান; কিংবা আমিই কি এই নগরের অগ্রজ সন্তান? যাই হোক, ব্যাপারটা একই।
কত পালটে গেছে এই জায়গা! গত চোদ্দ বছরে আমিও তো। যদি পুরোনো পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়, সে অবাক হয়ে বলবে, ‘আঃ, তুমি কি সত্যিই সরোজিনী?’
আশা, বন্ধু বরদা, আমার দুষ্মন্তর সঙ্গে দেখা হবে। আজ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যাব। এখন রাস্তায় প্লাবন নেমেছে—দূর থেকে উথাল-পাথাল ঢেউ এগিয়ে আসছে। মানুষ, মৌমাছি, গাড়িঘোড়া, কাকেদের বিশাল বিশাল ঢেউ। পশ্চিমা বাতাসে তরঙ্গ তুলে পথ হারাচ্ছে। ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করে, অন্তঃপ্রবাহের ফাঁদে পড়ে গেছে। ট্রাফিক পুলিশ তার জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে বটে কিন্তু কাজ হচ্ছে না তেমন। এ যেন সবাইকে হতচকিত করে দেওয়ার মতো ট্যাবলো। কিছুই যেন নাগালের মধ্যে নেই, ঘূর্ণিবায়ু শুষে নিয়েছে সব। জোয়ার শান্ত হোক, তারপর ঢেউয়ের আছাড়ে তীরের জঞ্জালের মাঝ থেকে পুরোনো খোলক কুড়িয়ে নেব এবং তার সঙ্গে বরদাকেও।
ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মাধবেত্তান এখন দু নং ওয়ার্ডের দু নং বেডে। বিশ্রাম নিচ্ছে। তার বন্ধুদের একজন আমাকে একটা খাবারের প্যাকেট দিয়ে বলেছিল, ‘অবসর সময়ে ঘরে বসে খেয়ো। দুজনের জন্যেই থাকল।’ তারপর মাধবেত্তানের ব্যাপারে হাত ধুয়ে ছাড়া পেয়ে সব চলে গেল।
আগে এটা ছিল কর্নেল রাজনের হাসপাতাল। নাম-ফলকটি বদলে গেছে। বাড়িটাও। যে জায়গাটি একই থেকে গেছে তা হল হাসপাতালের উলটো দিকে কর্পোরেশনের সেই পরিত্যক্ত পার্কটা যেখানে সার দিয়ে নিষ্ফুল গাছগুলো বেড়ে উঠেছে। তার চারদিকে লোহার রেলিং।
‘মানসিক রোগীদের হাসপাতাল’। বিশাল গেটের ওপর থেকে নিষ্প্রাণ শব্দগুলো একভাবে তাকিয়ে আছে। গেটের দরজা খোলা। চত্বরের উভয় দিকে রাখা গাড়ি সব নীরবে দাঁড়িয়ে। হাসপাতালে খদ্দেররূপী রোগী প্রচুর।
বড়ো গেট পেরোলে লোহার কোলাপসিবল গ্রিল আর একটা কাচের দরজার পরেই সরু সিঁড়িপথ। তার দুদিকে লোহাগ্রিলে আটকানো স্বচ্ছ কাচের দেয়ালে শহর জীবনের দৃশ্যাবলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। গ্রাম্য মানুষের কৌতূহল নিয়ে গালে হাত রেখে ভিতরটা দেখার চেষ্টা করলাম। হাসপাতালের উঁচু সিঁড়ির একটাতে একজন গার্ড বসে থাকবে, আমি ভাবতে পারিনি।
‘আপনি কী দেখছেন? ভিতরে আসুন।’
‘জোরে হাঁটুন’, একজন বলল। সিঁড়ি দিয়ে লোকজন ওঠানামা করছে। বড়োজোর তিনফুট চওড়া সিঁড়ি। আমি দ্রুত উঠলাম। করিডরে একগাদা লোক ভিড় করে আছে। কে রোগী, কে দর্শক, বোঝা দায়। ডাক্তারের চেম্বারগুলির দরজা বন্ধ। সেখানে দু তিনজন ডাক্তার রোগী দেখছেন।
ডাক্তার কর্নেল রাজনের রোগী দেখার একটিই বড়ো ঘর ছিল। পুরোনো বাড়িতে তার রোগী দেখার ঘরের সামনেই ছিল পার্কটি। সমস্ত ধরনের রোগীই সেখানে স্বাগত ছিল—রোগী এবং রোগের ধরনের কোনও বাছবিচার ছিল না। সংক্রমিত পচে যাওয়া কান, নড়া দাঁত, হাপরের মতো ওঠানামা করা বুক, পেটে খাদ্যসামগ্রীর উচাটন, বন্ধ্যা জরায়ু—এ সব সমস্যা নিয়ে আসা রোগী সমান যত্ন পেত; কেউই অবজ্ঞার ছিল না। ডা. রাজনের চেম্বারে সকলেরই উপশম হত, সদয় কথাবার্তা আর কড়া ওষুধের সাহায্যে। কখনও কখনও দূর গ্রাম থেকে আসা লোকজন তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইত। ডাক্তারবাবু তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভিনটেজ গাড়িটি নিয়ে তাদের সঙ্গে দ্রুত বড়ো রাস্তা দিয়ে ছুটতেন।
ডাক্তারবাবুর মেয়ে আমার সহপাঠী ছিল। একটা সময়ে বেশ কিছুদিন বাবার সঙ্গে তার দেখাই হত না। সে ছিল মাতৃহারা। তার দেখভালের জন্য ছিল এক বয়স্ক প্রায়ান্ধ পরিচারিকা।
বরদা অবশ্যই কাছাকাছি কোথাও থাকে। চোদ্দ বছরে কোনও পরিবার শেকড়শুদ্ধ উপড়ে যাবে, এটা অসম্ভব। নাগরিক জীবনের বাইরে কোনো জীবন বরদার কল্পনাতেও ছিল না। আমাদের ক্লাসে সেই ছিল একমাত্র মেয়ে যে রোজ সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত করত। গার্লস স্কুলের মেয়েরা সাইকেল চড়তে লজ্জা পেত। আমাদের ক্লাসটিচার এক সময় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ডাক্তারবাবুর মেয়ে বরদা সাইকেল চালালে তা ঠিকই আছে। কিন্তু কোনো চা-দোকানির মেয়ে যদি সাইকেল চড়ে সারা শহর হট্টিহট্টি করে ঘোরে সেটা ঔদ্ধত্য বলেই ধরে নিতে হবে। তার জন্য গ্রাম থেকে শহরে আসা-যাওয়ার তো বাসই আছে।
রাস্তার হুল্লোড় থেকে চোখ সরিয়ে ডাক্তারের কেবিনে ঢুকলাম।
‘আপনি কি শকুন্তলা, মাধবেত্তানের স্ত্রী?’
‘না, আমি সরোজিনী।’
‘তাহলে কি আমি ভুল জানতাম? মাধব যে বলেছিল…’
‘কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে সরোজিনী বলেই ডাকবেন।’
‘ওহো! কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ের পর স্ত্রীর নাম পালটানোর একটা প্রথা আছে। কিন্তু তাহলেও নামকরণের সময় কেউই তো আমাদের অনুমতি নেয় না।’
ডাক্তারবাবু হাসছিলেন। আমারও হাসা উচিত। আমি তাকে বলতে চাইলাম যে শকুন্তলাই মাধবেত্তানকে অসুস্থ করে তুলেছে, কেন-না আমি এক সময় মঞ্চে শকুন্তলার অভিনয় করেছিলাম। কিন্তু নিজেকে জিজ্ঞেস করা ভালো, সরোজিনী, তুমি কি মাধবেত্তানের সরোজিনী নাকি দুষ্মন্তর শকুন্তলা?
ডাক্তারবাবুর চেয়ারের পেছনের জানলাটায় কোনও লোহার শিক নেই; তা একটা খোলা জায়গা। অস্পষ্ট দৃষ্টিতে জানলার বাইরে চেয়ে দেখলাম—আমি যে স্কুলে পড়তাম, যেখানে পাঁচ বছর পড়েছিলাম, সেই স্কুল। সেটা ছিল মেয়েদের স্কুল যেখানে ছেলেদের ঢোকার অনুমতি ছিল না। হেডমিস্ট্রেস যিনি ছিলেন তার জন্ম গত শতকে হওয়া উচিত ছিল। স্কুলের বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কথা উঠলে তার মুখ গোমড়া হয়ে যেত। এমন উৎসব পালনের কোনও রীতি সেখানে ছিল না। সময় বদলে গেলে আমাদের সাহসী ক্লাসটিচার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেটা ছিল আমাদের স্কুলের শতবার্ষিকী।
‘তাই?’
‘হ্যাঁ। খবরকাগজ থেকে তা জেনেছিলাম।’
খবরকাগজ শব্দটা শুনে হেডমিস্ট্রেসের মুখ জুড়ে আবার মেঘ জমল—‘এর কি প্রয়োজন আছে? তাহলে সাংবাদিকের দল হরদম স্কুলে ঢুকবে আর বেরোবে।’
‘কিন্তু তারা এটাও জানবে কেন আমরা শতবার্ষিকী উদযাপন করছি না।’
হেডমিস্ট্রেস নিমরাজি হলেন। তারই ফল হল ‘শকুন্তলা’ নাটকের মঞ্চায়ন।
ডা. রাজনের স্বাস্থ্যবান কন্যা বরদা স্বেচ্ছায় দুষ্মন্তর ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজি হল। সে যতটা সম্ভব বাড়ির বাইরে সময় দিতে রাজি হল। বরদা ঘোষণা করল, আমিই শকুন্তলার অভিনয় করব। আমি তো চোখে অন্ধকার দেখলাম। স্টেজে উঠতে হবে? হা ঈশ্বর!
আমাকে ভয়ে কাঁপতে দেখে বরদা জড়িয়ে ধরল, ‘তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো সঙ্গে আছি।’
‘আমার তো পাঠ মনে থাকে না।’
‘নাটক মুখস্ত করে করতে হয় না।’
‘তাহলে?’
‘সময় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।’
প্রথম মহড়া পুরো ফ্লপ। আমার গলায় শব্দগুলো দলা পাকিয়ে একাকার।
‘না, আমাদের আর কোনও মহলার দরকার নেই। শুধু এই ব্যাপারে ধ্যান দাও।’ বরদা বলল।
লাঞ্চ-ব্রেকের সময় ওই দোকান থেকে—ওহো, দোকানটি তো আর সেখানে নেই! বদলে মার্বেলের দেওয়াল দেওয়া মারুতি শো-রুম হয়েছে। ভিতর থেকে নানারঙের গাড়ি পথচারীদের হাতছানি দিচ্ছে। আগে এখানে একটা নীচু ছাদের বাড়ি ছিল। সংলগ্ন আউটহাউজে সাইকেল ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা ছিল। বরদা সেখান থেকে ভাড়ায় সাইকেল নিত। সে তার সাইকেল ক্যারিয়ারে বসিয়ে আমাকে সাহসী করে তুলেছিল। তখনও তার বোঝা উচিত ছিল, এ জীবনে আমি কখনোই সাইকেল চালাতে পারব না।
আমাকে ক্যারিয়ারে বসিয়ে সমুদ্রের হাওয়ায় জড়াপট্টি খেতে বরদা বিচে চলে যেত। প্রথম প্রথম জেলেদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ঘিরে ধরত, টায়ারের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ফচকেমি করত আর সাইকেলটিকে নোংরা করতে চাইত। একবার বরদা তাদের একজনকে চড় মেরে অন্যদের মিষ্টি হাসিতে প্রলুব্ধ করল। আমাদের গন্তব্য ছিল বিচের কাছাকাছি চাভোক কাঠের জঙ্গল। সেখানে সাইকেল দাঁড় করিয়ে আমরা বালির ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিলাম। আমার চটি পরা পায়ে যাতে কাঁটা না ফুটে যায়, আমাকে আদর করতে করতে সেই সব কাঁটা খুঁজছিল দুষ্মন্ত আর সেই সময় আলতোভাবে আমার তেলতেলে গালে চুমু খেল। সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে নাটক-থিয়েটারই জীবন।
স্কুলে আমাদের নাটক ‘শকুন্তলম’ মঞ্চে ঝড় তুলে দিল। পরদিনই গরমের ছুটি পড়ে গেল। আমি আমার গ্রামের ছোট্ট বাড়ির চা-দোকানের পেছনেই থেকে গেলাম।
এক ঘুমঘুম বিকেলে বারান্দায় যেন বাজ পড়ল।
‘এই মেয়ে… সরোজিনী…।’
সত্যিই কি বাবা ডাকছিল? আমি আমার জায়গা থেকে একটুও নড়লাম না।
মা ইতস্তত করে সামনের ঘরের দিকে গেল।
‘এই যে, এটা তোমার মেয়ের…’
‘কী এটা?’
‘প্রেমপত্র।’
‘হা ভগবান।’
‘আমি তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম, মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ো না…।’
এটা দুষ্মন্তর কাছ থেকে আসা প্রেমপত্র।
‘কে এই দুষ্মন্ত, বল? এটা কি কোনো গোপন নাম?’
‘না।’
‘এই ছেলেটা তোকে চিঠি লেখে কেন?’
‘ছেলে নয়, মেয়ে।’
আমার ভাই ফিক করে হেসে ফেলল। ছুটে গিয়ে ওর দুই গাল থাপড়িয়ে রাগ মেটালাম।
একের পর এক দুষ্মন্তর কাছ থেকে চিঠি আসতে থাকলেও আমি তার একটিরও উত্তর দিইনি। বাবার ভয় ছিল ওই চিঠিগুলো আমাকে হয়তো গর্ভবতী করে দেবে। মাধবেত্তান ছিল বাবার চা-দোকানের সহকারী। বাড়ির আঙিনায় মেরাপ বাঁধা হলে বাড়ির ধান মাড়াইয়ের কিষান আম্মালু বিড়বিড়িয়ে বলল, ‘খুবই তাড়াহুড়ো হয়ে গেল… মেয়েটার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হওয়া অব্দি বাড়ির লোক অপেক্ষা করতে পারত।’
বিয়ের রাত্রে মাধবেত্তান তার কুয়ো থেকে অবিরাম জল- তোলা খসখসে হাতে আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ‘তার চিঠি কি আবার আসবে?’
প্রথম প্রথম আমার কান্না পেত খুব। কিন্তু না, সে যখন তাকিয়ে থাকত আমি কাঁদতাম না। সেটা খুব অমর্যাদাকর হত।
‘চিন্তা কোরো না। ওসব ভুলে যাও।’
‘কী সব?’
‘চিঠি। দুষ্মন্তর চিঠি।’
তাকে চোখের কোনায় আটকে নিয়ে আকাশে তুলে ফেললাম। সে ভয় পেয়ে গেল।
‘লক্ষ্মীটি শোনো। ছেলেটা সম্পর্কে আমি আর কিছু জানতে চাইব না। আর নয়, ঠিক আছে?’
কিছুক্ষণ পর সে আবার জিজ্ঞেস করল।
‘তোমাকে শকুন্তলা বলে ডাকতে পারি?’
‘না।’
‘ওই নামটি তোমাকে বেশ মানায়।’
‘তোমাকে “না” বললাম তো?’
আর আজ মাধবেত্তান ডাক্তারবাবুকে বলেছে যে তার স্ত্রীর নাম শকুন্তলা। লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠল। কে বলেছে, মাধবেত্তান অসুস্থ? হ্যাঁ, আমি বলেছি।
আমাদের বিয়ের পরদিন থেকে মাধবেত্তান পান চাবিয়ে ঠোঁট লাল করতে লাগল।
‘ওর এই নতুন অভ্যেস কবে থেকে?’ বাবা মায়ের কাছে জানতে চাইল।
‘আগে কখনও ওকে এক সেকেন্ডের জন্য ছেড়েছ যে খানিক হাঁফ নিয়ে মাথা চুলকোবে আর একা একা পান খাবে?’
পান চিবোনোর সময় মাধবেত্তান আমার কাছে জানতে চাইত: ‘দেখো, আমার ঠোঁটদুটো লাল হয়নি?’
‘হুঁ।’
‘গাঢ় লাল?’
‘নিজেই গিয়ে আয়নায় দেখো না?’
এরপর একদিন সে আমাকে বলল, ‘পান খাওয়া সাহসী পুরুষের লক্ষণ। তাদের ঠোঁটদুটো এমন লাল হয়ে থাকে যেন মনে হয় রক্ত পান করেছে।’
আর একদিন সে শহর থেকে একটা লাল দাঁতের মাজনের কৌটো নিয়ে এল। তা দিয়ে ভালো করে দাঁত রগড়ে লাল থুতু ফেলে সে আমাকে বলেছিল: ‘আমি এখন ভীম। দেখোনি ভীম কীভাবে দুঃশাসনের পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে তার রক্ত পান করে কেমন থুঃ করে ছিটিয়েছিল? সেই সময় তুমি কি কোনও কথাকলি নাচ আদৌ দেখেছ? ওই বোকা-বোকা নাটকই তো তোমার পছন্দ।’
আমি যখন তার দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি, সে হঠাৎ মুখটুখ ধুয়ে চায়ের দোকানের দিকে হাঁটা দিল।
গত রাত্রে এই অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে আমি জানলাম। মাধবেত্তান আমার চুল বাঁধতে এল। তার হাতে এক দলা লাল থুতু। মনে হল, সময় আগত।
বাবা মাকে বলছিল, ‘চায়ের দোকানেও ওর আচরণ কেমন অদ্ভুত লাগে।’
আর এভাবেই আমি এখানে এসে পৌঁছলাম। তাকে ডা. রাজনের হাসপাতালেই আনতে চেয়েছিলাম। তিনি যা বলবেন, তাই করব। আমার চেনা তিনিই একমাত্র ডাক্তার যিনি সমস্ত রোগের চিকিৎসা করেন। ডাক্তারবাবু অর্থাৎ বরদার বাবা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। এ ছাড়া বরদাকে দেখার সুপ্ত ইচ্ছেটি তো মনের মধ্যে ছিলই যদিও এত বছর ধরে তাকে মনের বাইরেই রাখতে চেষ্টা করেছি।
হাসপাতাল ক্যান্টিন থেকে মাধবেত্তানের জন্য কিছু স্ন্যাকস কিনতে হবে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মাধবেত্তান মাথা তুলল। পান-ছাড়া মুখ তার পাংশু দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এক অদ্ভুত জীব। আমাকে ওয়ালেট বের করতে দেখে সে বলল, ‘তুমি কি পান কিনবে?’
‘আগে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করি।’
‘কী?’ পাশের বেডের রোগীর প্রশ্ন ভেসে এল। ‘এই ওয়ার্ডে যারা আছে তাদের এমন কী রোগ আছে যে পান খাওয়া বারণ?’ প্রশ্নকর্তা যুবক একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ছিল। ম্যাগাজিনটাকে উলটে ফেলে মজাসে ছবিগুলো দেখছিল। ‘বোন, আমাকে দুটো টফি এনে দেবে, প্লিজ?’ অনুনয়ের সুরে বলল সে।
‘হ্যাঁ দেব।’ আমি বললাম।
‘দাঁতের মাজন কিনতে ভুলো না কিন্তু।’ মাধবেত্তান মনে করিয়ে দিল।
ঘুরে চলতে শুরু করার সময় তার গলা আমার কানে এল, ‘রামেশা, বলো, দুষ্মন্তর চাইতে ভীম উৎকৃষ্ট নয়?’
আমার শিরদাঁড়া বেয়ে কাঁপুনি নামল।
সিঁড়ির ধাপে বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গার্ড জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাচ্ছেন?’
‘দাঁতের মাজন আর কলা কিনতে।’
‘এখানকার ক্যান্টিনে তো সবই পাওয়া যায়।’
তার উপদেশে পাত্তা না দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম। কোলাপসিবল গেট এঁটে বন্ধ করা ছিল। একজনও তা গলে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।
বড়ো রাস্তার হুল্লোড় তখনও কমেনি আর প্রিয় রাস্তাজুড়ে মানুষের ঢল। বরদার বাড়ি এই রাস্তার ওপারের একটা ছোটো পথের ওপর যা পশ্চিমপানে মুখ করে থাকা স্কুল চত্বর সংলগ্ন। সেই ছোট্ট পথটি কি বড়ো রাস্তা হয়ে গেছে? ট্রাফিকের ঢেউ কি বরদার বাড়ি, সেই বিশাল গাছটি যা আমাকে ছায়া দিত, সে সব উপড়ে নিয়ে গেছে? এই জনসমুদ্র পেরোব কীভাবে? মানুষ ঠেলাঠেলি করে জেব্রা ক্রসিং পায়ে দলে এগোচ্ছে—পথচারী আর যানবাহনের মধ্যে এক সীমাহীন দৌড় প্রতিযোগিতা চলছে।
আমার সামনে-পেছনের লোকজন রাস্তার অপর প্রান্তে পৌঁছনোর জন্য ধৈর্যহারা হয়ে অপেক্ষা করছে। আমি সাহসে ভর করে তাদের সঙ্গে রাস্তা পেরোলাম।
কিছুক্ষণের জন্য আমরাই পাহারাদারি করে একে অপরের ঢালের কাজ করলাম—যারা অন্য জায়গা থেকে এসে কোনও অচেনা গন্তব্যে যেতে উদ্যত।
বরদার বাড়ির রাস্তা এখন আমার সামনে পড়ে আছে। একইরকম। দুপাশে ঠেলাগাড়ি সব রাখা আছে। শুধু রাস্তাজুড়ে খাবলানো গর্তের সংখ্যা বেড়েছে। দুপাশের বাড়িগুলো বাচ্চাদের স্কুলের মতো গাদাগাদি দম আটকানো, তবু্ও বেশ উচ্ছল।
প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম বরদার বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে। বার্নিশ করা উজ্জ্বল পুরোনো কাঠের দরজা জানলা সব বিউটি পার্লার ফেরত মেয়েদের মুখের মতো দেখাচ্ছে—সাজগোজে পাণ্ডুবর্ণ। দরজা জানলার স্বচ্ছ পর্দাগুলোর মাঝ দিয়ে আলগা ঘরটা দেখা যাচ্ছে। মনে হল বাড়িটা মেয়েদের হস্টেল হয়ে গেছে। বাড়ির পেছনের উঠোনে দড়িতে মেয়েদের কাপড়চোপড় মেলা। দুটো মেয়ে সেই সব শুকনো জামাকাপড় টেনে নামিয়ে হাতের ফাঁকে রাখছে। সেই গুরুগম্ভীর মেয়ে দুজন গেট খোলার আওয়াজে পেছন ফিরে তাকাল।
যেখানে ডা. রাজনের নেমপ্লেটটি ঝোলানো থাকত সেই জায়গাটি দেখে মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট আয়তাকার জানলা। প্লেটটি আর সেখানে নেই কিন্তু দেওয়ালে পেরেকের দাগগুলো ফাঁকা কোটর বানিয়ে রেখেছে।
বরদা কি এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে? সে কি বিয়ে-থা করেছে, পুরনো স্মৃতিসব পেছনে ফেলে এই বাড়ি বিক্রি করে দূরে কোথাও চলে গেছে? আমার ভাবনা-জর্জর মন তাকে কারও স্ত্রীর ভূমিকায় ভাবতেই পারছে না।
ক্যাটকেটে লিপস্টিক লেপা তৃতীয় মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমাকে দেখে মৃদু হাসল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম:
‘বরদা কোথায়?’
‘কে?’
‘বরদা, যে এখানে থাকত। ডা. কর্নেল রাজনের মেয়ে।’
‘ওহো, আপনি ম্যাডামের কথা বলছেন? তিনি কোথাও যাননি। এখানেই থাকেন।’
মেয়েটা চোখের ভুরু বাঁকিয়ে আমাকে আগাপাশতলা জরিপ করে নিল। তারপর আর কোনও কথা না বলে পর্দার আড়ালে মিলিয়ে গেল।
দরজায় বরদাকে দেখে আমার হৃৎস্পন্দন থমকে যাওয়ার জোগাড়।
‘বরদা, বরদা, এই যে আমি… তোমার… শকুন্তলা!’
বরদা দুই হাত মেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। হাততালুতে আমার মুখটি ধরে বলল,
‘কদ্দিন পর, প্রিয় বন্ধু!’
সার দেওয়া জানলা ফুঁড়ে আমাদের দেখতে থাকা চোখগুলোর বিষয়ে সচেতন হয়ে লজ্জিত হলাম খুব। আমার মধ্যে একটা আগুন জ্বলতে শুরু করল আর শরীরের প্রতিটি লোম যেন জ্বলন্ত শিখায় পরিণত হল।
বরদা আমাকে তুলে ভিতরে নিয়ে গেল।
আমি শুকনো ঠোঁট নিয়ে বরদার ঘরের একটা সোফায় বসলাম। চোখ জ্বালা করতে লাগল।
একটা বড়ো গ্লাসে সরবত ঢেলে পাইপসহ আমার ঠোঁটে বসিয়ে দিল সে।
‘এটা খেয়ে নে। তোর ওজন কমে গেছে।’
মুখ দিয়ে কথা সরল না আমার। গলার মঙ্গলসূত্রের দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইল:
‘তোর বিয়ের খুব তাড়াহুড়ো ছিল, তাই না? এত ব্যস্ত যে আমার চিঠিগুলির উত্তর দেওয়ারও সময় পাসনি।’
আমি চুপ মেরে থাকলাম।
‘দেখ, আঙুলের ফাঁকে কেমন ময়লা জমেছে। আজ বোধহয় স্নানও করিসনি। পরনের জামাকাপড়ের হাল দেখেছিস? কী নোংরা!’
আমি নখ দিয়ে ময়লা সুতির শাড়িটায় আঁচড়াতে থাকলাম। সে আমার চিবুক তুলে বিরক্তি সহকারে বলল:
‘বোকা কোথাকার! তুই যে এমন বুদ্ধু তা আমি কখনোই ভাবিনি।’
আমার সর্বাঙ্গের চামড়া কুঁচকে উঠল। আমি যেন একটা পোকা হয়ে গেলাম। বরদার গোলাকার গাল তার উঁচু চোয়ালের হাড় আরও ফুলিয়ে দিয়েছে যেন। কানের নীচ দিয়ে হাত গলিয়ে চুল ঠিক করে সে বলল,
‘আর তোকে আমি যেতে দেব না।’
এক মধ্যবয়স্কা একটা ট্রেতে দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।
‘ওইখানে রেখে চলে যাও… আজ তোমাদের কাউকেই আর দেখতে চাই না।’ বরদা বলল।
সে চলে যেতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে দরদালান জুড়ে পুরুষ কণ্ঠ আর পায়ের শব্দ মিইয়ে এল।
‘বরদা, এখানে তুই কী করিস?’
‘ব্যবসা।’
সে আমাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল।
আমার মন সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কেলাসের মতো চকমকিয়ে উঠল।