দিবারাত্রির মানিক –
আজ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামের একটি আগুনের জন্মদিন।
তাঁকে নিয়ে আমার একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য।
দিবারাত্রির মানিক
বিনোদ ঘোষাল
শৈশবে আদর করে লোকে ডাকত কালোমানিক। সাহিত্যজীবনে নিজেই নাম নিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
কুস্তির আখড়ায় মুগুর ভাঁজতেন। গুন্ডার দল সামলেছেন একা হাতে।
ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দুরন্তপনারঅন্ত নেই।
এই একই মানুষ আবার জ্যোৎস্নারাতে আড়়বাঁশি বাজাতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত-অতুলপ্রসাদী গাইতেন।
তাঁর সাহিত্যসাধনা, সংসারযাপন থেকে চরম দারিদ্রের সঙ্গে সহবাস, তাঁর গল্প-উপন্যাসের কাহিনির মতোই রূঢ়। কঠিন।
তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কী করে বাঁচল যে…
তখন বয়স মাত্র চার। হলদি নদীর পাশেই একটা খালের এক হাঁটু কাদাজলে নেমে এক হাতে লাল কাঁকড়া ধরছেন।
আর অন্য হাতে ধরা কাচের বয়ামে সেই কাঁকড়া ভরে ফেলছেন। আচমকাই আঠালো এঁটেলমাটিতে পা’দুটো গেঁথে গেল।
আর নড়াচড়ার উপায় নেই।
চটচটে কাদামাটি ক্রমশ ভেতরে টেনে নিচ্ছে। একটা বাঁশ ধরে কোনও মতে নিজেকে টেনে তোলার চেষ্টা করলেও চোরাবালির মতো সেই মাটির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আর বুঝি বাঁচার আশা নেই।…তারপর কী যে হল, কী করে প্রাণ বাঁচল আর স্মৃতিতে নেই।
অনেক বছর পেরিয়ে মানিক বড় হয়ে বাড়ির লোককে, পরিচিতদের জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। তাহলে কি আদৌ কিছুই ঘটেনি এমন?শুধুই কল্পনা?
তা হলে বার বার কেন মনের মধ্যে অষ্পষ্টভাবে ঘুরতে থাকে ওই স্মৃতিটুকু আর অশান্ত করে তোলে তাঁকে?
ঠিক করে ফেললেন আবার যেতে হবে ছোটবেলার সেই জায়গায়। গেলেন। কিন্তু তত দিনে নদীর ধারের সেই খালের পরিবেশ অনেক বদলে গেছে।
পরিচয় হল খালপাড়ে দর্মার ঘরে থাকা এক বুড়োর সঙ্গে। ছেঁড়া সবুজ কোট পরা সেই বৃদ্ধ বড্ড বকবক করে। তাকে এড়িয়ে একা হলেন।
সারাটা দিন ওই খালের ধারেই ভাবতে ভাবতে অন্ধকার নামল একসময়। পাড়ে রাখা একটি নৌকোয় গিয়ে বসলেন তিনি। আবার ভাবনা।
ভাবতে ভাবতে একসময়ে চোখ বন্ধ হয়ে গেল ঘুমে। চোখ যখন খুললেন, দেখলেন তিনি এক হাঁটু পাঁকের মধ্যে। সেই সবুজ কোট বৃদ্ধ তাকে কাদা থেকে টেনে হিঁচড়ে ডাঙায় তুলে ‘বাবু বাবু উঠুন’ বলে গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। সম্বিৎ ফিরল মানিকের। কিন্তু আবার পাঁকের মধ্যে গেলেন কী করে!
বৃদ্ধ বলল, ‘‘আমার রাতে ঘুম আসে না। বাইরে বসে তামাক টানছিলাম। চাঁদের আলোয় দেখলাম আপনি হাঁটতে হাঁটতে ওই খালে নেমে যাচ্ছেন। প্রথমটায় বুঝতে পারিনি, তারপর দৌড়ে গিয়ে দেখি আপনি ডুবে যাচ্ছেন। ওহ্! আমি না থাকলে আজ যে কী হত!’’
এইটুকু বলে একটু দম নিয়ে সেই বৃদ্ধ যা বললেন, তা শুনে শিউরে উঠলেন মানিক।
‘‘জানেন বাবু, আজ থেকে অনেক বছর আগে, ঠিক আপনার মতো করেই একটি বাচ্চা ছেলে ওই পাঁকে ডুবে যাচ্ছিল। তাকেও এইভাবে বাঁচিয়েছিলাম। কাদের ছেলে জানি না। পরে আমাকে অনেকগুলো টাকা বখশিশ দিয়ে গেছিল ছেলেটি।’’
আর মানিকের মনে পড়ল, তাই তো! ছেলেবেলায় বাবার পকেট থেকে অনেকগুলো টাকা চুরি করে কাকে যেন দিয়ে এসেছিল, আর সেই চুরি নিয়ে বাড়িতে হুলুস্থুলও হয়েছিল খুব। কে চুরি করেছে শেষ পর্যন্ত জানা যায়নি কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত বাড়ির সকলে সেই চুরি নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু ওই পাঁকে ডুবে যাওয়ার কাণ্ডটা রহস্যজনক ভাবেই বেমালুম চেপে গেছিল সকলে। আজ সেই একই ঘটনার হুবহু পূনরাবৃত্তি! একই মানুষ আবার প্রাণ বাঁচাল তার! এমনও হয়! মনে পড়ছে, মনে পড়েছে সব!
স্মৃতি ঘেঁটে ফেলে আসা অতীতকে এইভাবে খুঁজে চলার ঘটনা বারবার ঘটেছে মানিকের জীবনে। বলব সেই কথা।
নিজের নাম নিলেন নিজেই…
চার ভাইবোনের পর জন্ম হল ঘুটঘুটে এক কালো ছেলের। অমন গায়ের রং দেখে আঁতুড় ঘরেই নাম দেওয়া হল কালোমানিক।
বামুনের ছেলে। রীতমতো গণক ডেকে জন্মঠিকুজি তৈরি করা হল। ঠিকুজিতে নাম রাখা হল অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নামে কেউ কোনও দিনও ডাকল না।
এমনকী বাবা হরিহর সাধ করে ছেলের নাম রাখলেন প্রবোধকুমার। সেই নামও আড়ালেই থেকে গেল। ভালবেসে কালোমানিক বলেই ডাকত সকলে।
তারপর যা হয়, বয়স বাড়তে কালোমানিক থেকে কালো গেল খসে। পড়ে রইল শুধু মানিক। ওই নামেই জীবনের প্রথম গল্প ‘অতসী মামী’ ছাপা হয়েছিল।
তখন গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। একদিন কলেজ ক্যান্টিনে বন্ধুদের সঙ্গে তুমুল তর্ক। এক বন্ধুর লেখা গল্প কোনও একটি নাম করা পত্রিকা থেকে অমমোনীত হয়ে ফেরত এসেছে। সেই বন্ধু মহা খাপ্পা হয়ে বলল, বড় পত্রিকাগুলি নামী লেখকদের লেখা ছাড়া ছাপায় না।
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন মানিক।— ‘‘এটা হতেই পারে না। তুমি ভুল বলছ। তোমার গল্প ভাল হয়নি বলেই তারা ছাপেনি। পছন্দ হলে নিশ্চয়ই ছাপত।’’
বন্ধুও পাল্টা নিলেন, ‘‘প্রমাণ করে দেখাতে পারবে?’’
‘‘বেশ, আমি আগামী তিন মাসের মধ্যে একটা গল্প লিখে কোনও নামী পত্রিকায় ছাপিয়ে দেখাব।’’
তিন মাস নয়, তিনদিনের মধ্যে একটা গল্প লিখে ফেললেন। গল্পকারের নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে গিয়েও থমকালেন।
জীবনের প্রথম গল্প। সম্পাদকের পছন্দ হবেই সে বিষয়ে নিশ্চিত। কিন্তু বারো তেরো বছর বয়সের মধ্যেই বাংলার সেরা সাহিত্যগুলো যার পড়া হয়ে গেছে সেই মানিক কিন্তু বুঝেছিলেন ‘অতসী মামী’ আসলে ‘অবাস্তব রোম্যান্টিকতায় ভরা’।
সেই সংকোচেই প্রবোধকুমারের বদলে লিখলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সেই গল্প নিয়ে নিজেই সটান হাজির ‘বিচিত্রা’ পত্রিকার দফতরে।
সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ সেই সময় দফতরে ছিলেন না। তার জায়গায় বসেছিলেন আরেক দিকপাল সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। স্মৃতিকথায় অচিন্ত্যকুমার লিখছেন, ‘‘একদিন বিচিত্রার দফতরে কালোপানা একটি লম্বা ছেলে এল। বলল গল্প এনেছি। বললাম, দিয়ে যান। সেই ছেলে লম্বা হাত বাড়িয়ে গল্পের পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলল, এই যে রাখুন। এমন ভাব যেন এখুনি ছাপতে দিয়ে দিলে ভাল হয়। চোখে মুখে আত্মবিশ্বাস চুঁইয়ে পড়ছে। গল্প জমা দিয়ে সে চলে গেল। আমি তারপর এমনিই গল্পে একবার চোখ বোলাতে গিয়ে চমকে উঠলাম। এ যে রীতিমতো দুর্দান্ত গল্প!’’
সেই গল্প প্রকাশ তো পেলই, বাংলার পাঠকমহলেও হইহই পড়ে গেল। বিচিত্রার সম্পাদক খোঁজখবর নিয়ে ছুটে এলেন মানিকের সঙ্গে দেখা করতে। লেখার সাম্মানিক কুড়িটা টাকা হাতে দিয়ে অনুরোধ করলেন, ‘‘আপনি আবার গল্প দিন আমাদের।’’
ইচ্ছে ছিল ত্রিশ বছরের আগে কোনও দিন গল্প লিখবেন না, কিন্তু কুড়ি বছর বয়েসেই বাজি রেখে গল্প লিখে এমনই বিখ্যাত হয়ে গেলেন যে সেদিন আবার গল্প লিখতে রাজি হতে হল, আর সেদিনই ঠিক হয়ে গিয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিয়তি।
দস্যিপনার শেষ নেই…
একেবারে ছোট বয়স থেকেই সাংঘাতিক দস্যি।
ফলে একের পর এক দুর্ঘটনা। হাঁটতে শিখেই বাড়ির আঁশবটিতে নিজের পেট কেটে প্রায় দুই ফালা করে ফেলেছিলেন।
ডাক্তারবাবু সেলাই করলেন। সেই সেলাই নিয়েই পরদিন ওই হাসপাতালেই দাপাদাপি শুরু। দস্যিপনার সঙ্গে ছিল এক উদ্ভট স্বভাব।
যতই চোট-ব্যথা লাগুক কিছুতেই কাঁদতেন না। কাঁদার বদলে বিচিত্র সুরে কালোয়াতি গান ধরতেন।
ফলে বাড়ির বড়রাও কেউ বুঝতে পারতেন না, মানিক আবার কোনও বিপদ ঘটাল কি না।
একবারের ঘটনা। সবার অলক্ষ্যে উনুন থেকে চিমটে দিয়ে জ্বলন্ত কয়লা তুলে খেলতে গিয়ে সেই কয়লা পড়ল পায়ের গোড়ালির পাশে। ব্যস, কালোয়াতি গান শুরু। কেউই বুঝতে পারে না আসলে কী হয়েছে।
তারপর মাংস পোড়ার গন্ধ পেয়ে সকলে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে চোখের জলে গলা বুক ভেসে যাচ্ছে মানিকের, কিন্তু গলায় গান আর পায়ে গর্ত হয়ে গেঁথে যাওয়া গনগনে কয়লার টুকরো। সেই এক ইঞ্চি পোড়া দাগ আর জীবনে ওঠেনি।
আরেকবার। মানিক তখন ক্লাস সেভেন। ম্যালেরিয়ায় কাবু। স্কুল যাওয়া বন্ধ।
এদিকে কালীপুজোর বাকি আর কয়েকদিন। বাড়ি বসে কী করা যায়? মাথায় বুদ্ধি এল পটকা বানালে হয়।
ভাবামাত্র ছোট দুই ভাইকে নিয়ে কাজ শুরু। ন্যাকড়ার ফালিতে পাথরকুচি পেঁচিয়ে বাঁধছে মানিক। পাশে কাচের শিশিতে রাখা বারুদ। দাদার পিছনে বসা এক ভাইয়ের কৌতূহল হল বারুদ কেমন ভাবে জ্বলে তা দেখার।
মেঝেতে কিছুটা বারুদ ঢেলে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ছোঁওয়ানো মাত্রই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ।
কাঁচের শিশি ফেটে তার কুঁচি তিন ভাইয়ের গোটা শরীরে।
ধোঁয়া কাটার পর দেখা গেল তিন ভাই বারান্দায় শুয়ে ছটফট করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বারান্দা। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনকেই নিয়ে যাওয়া হল ডাক্তারখানায়।
অতিরিক্ত রক্তপাতে তিনজনই কাহিল। ছোট ভাইয়ের অবস্থা সব থেকে সঙ্গিন। সরু ফুটো করে কাচ শরীরে ঢুকেছে। আগে শলা ঢুকিয়ে কাচের অবস্থান বুঝতে হবে, তারপর মাংস কেটে মুখ বড় করে কাচ বার করতে হবে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার।
ডাক্তারবাবু বললেন, ‘‘মানিক তুমি তিন ভাইয়ের মধ্যে সব থেকে বড়। আর এইভাবে বাজি বানাতে গিয়ে তুমি খুব অন্যায় করেছ, তাই তোমাকে দিয়েই শুরু করব। কিন্তু একটা কথা, যতই ব্যথা লাগুক, টুঁ শব্দ করবে না। তুমি যদি চেঁচামেচি করো, তা’হলে তোমার দুই ভাই আরও ভয় পেয়ে যাবে।
শুরু হল চিকিৎসা। দাঁতে দাঁত চেপে চোখ বুজল মানিক। ডাক্তারবাবু ক্ষতর ভেতর লোহার শলা ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে কাচ খুঁজলেন, তারপর কাঁচি দিয়ে ওই কচি হাতের চামড়া মাংস কেটে কাচের টুকরোগুলো একে একে বার করলেন।
ততক্ষণ মানিক পুরো চুপ।
শেষ ব্যান্ডেজটা বেঁধে ডাক্তার অবাক হয়ে বাবা হরিহরকে বললেন, ‘‘আশ্চর্য ছেলে তো আপনার!এত ব্যাথাতে সত্যিই একটু শব্দ করল না!’’
সেদিনের ডাক্তারবাবুর ওই কথার উত্তর দিয়েছেন মানিক অনেক পরে। স্মৃতিকথায় লিখছেন—
‘‘ডাক্তার বা আত্মীয়স্বজন বোঝেনি ব্যাপারটা। তাই তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। বীরত্ব বা অসাধারণ সহ্যশক্তির কোনও পরিচয়ই আমি সেদিন দিইনি। আমি চোখ বুজেছিলাম আহত রক্তমাখা ভাইদুটির চেহারা, যন্ত্রণায় বিকৃত কাতর তাদের মুখ মনের চোখের সামনে রাখার জন্য।’’
স্বভাব তো ছোটবেলা থেকে ডাকাবুকো ছিলই, তার ওপর জোয়ান বয়সে কুস্তির আখড়ায় গিয়ে নিয়মিত শরীরচর্চা, মুগুর ভেঁজে শরীরটাও হয়ে গিয়েছিল লোহার মতো। ভয়ডর নেই।
একবার গ্রামের এক গুন্ডা মানিকের ছোটভাই লালুকে জোর করে ধরে আটকে রেখেছিল।
সেই খবর মানিকের কানে পৌঁছানো মাত্র গুন্ডাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ।
‘‘হিম্মৎ থাকলে মাঠে এসো। মোকাবিলা হবে।’’
গুন্ডা এল সদলবলে আর ময়দানে মানিক একা। একাই একশো। সব ক’টাকে এমন তুলোধোনা করেছিল যে কয়েক দিনের জন্য তাদের আস্তানা হয়েছিল হাসপাতালের বিছানা।
কেউ কল্পনাও করতে পারেনি এমন সিংহের মতো শক্তিমান মানুষটাই আর কিছু বছর পর থেকে ক্ষয়ে ধুঁকতে শুরু করবে!
হঠাৎ নিখোঁজ…
বাঁশি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। মাঝেমাঝেই বাঁশি হাতে বেরিয়ে পড়েন একা। আদাড়েবাদাড়ে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান। সঙ্গে গান আর বাঁশি। বাড়ি ফেরার হুঁশ থাকে না।
ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান কিংবা নৌকোর মাঝিদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে আড্ডা।
এক-এক দিন থেকেও যান তাঁদের সঙ্গে। তখন চোদ্দ কী পনেরো বছর বয়স হবে, হঠাৎই বাড়ি থেকে নিখোঁজ। কয়েক দিন পেরিয়ে গেল মানিকের খবর নেই। বাড়ির সকলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। মা কেঁদেকেটে অস্থির।
অনেক খোঁজের পর মানিককে পাওয়া গেল টাঙ্গাইলের নদীর ধারে যে নৌকোগুলো নোঙ্গর করা রয়েছে, তাদের মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে। দুই বেলা তাদের সঙ্গে গল্প,গান খাওয়াদাওয়া করে দিব্যি রয়েছে। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার বাড়ি ফেরানো হল। সেদিন কেই বা জানত মাঝির সঙ্গে, নদীর সঙ্গে ছেলেটির এই আত্মীয়তাই একদিন জন্ম দেবে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ নামের এক উপন্যাস!
খাটের নীচে নরুনের দাগ
ফেলে আসা জীবনের ছবি মানিককে তাড়া করে গেছে আজীবন।
সেই ছবিগুলোকে মনে মনেই জোড়া দিয়ে একটা গোটা ঘটনাকে সাজাতে চেষ্টা করতেন। সাজিয়ে তারপর বাস্তবে তা ঘটেছিল কি না যাচাইয়ের চেষ্টা।
একবারের ঘটনা বলি।
তখন মানিক অস্থির হয়ে উঠেছেন একটি ভাবনাকে নিয়ে। সারাক্ষণ তার মনের মধ্যে আসছে শৈশবের একটি মুহূর্ত। কোনও একটি বাড়িতে গেছেন। সেই বাড়ির একটি ঘরের খাটের তলায় ঢুকে হাতে একটি নরুন দিয়ে খাটের নীচের দিকে দাগ কাটছেন।
ব্যস, এইটুকুই। আর কিছু মনে নেই।
কার বাড়ি, কোথায় সেই বাড়ি কিছুই মনে আসছে না। কিন্তু যেভাবেই হোক তাকে জানতেই হবে।
একদিন রওনা দিলেন বাড়ি থেকে মাইল দশেক দূরে এক আত্মীয়ের বাড়ি।
এত দিন পর তাদের কালোমানিক এসেছে। পরিবারের সকলে খুব খুশি। খাটে বসিয়ে গল্প করছেন বাড়ির কর্তা।
মানিক কথা বলছেন, তাদের কথা শুনছেন ঠিকই কিন্তু শুধু মনে হচ্ছে এই ঘরটাই! কিন্তু এখন তো আর সে ছোটটি নেই যে ইচ্ছে হলেই হুট করে খাটের তলায় ঢুকে পড়া যাবে। অপেক্ষায় থাকলেন কখন একটু একা হবেন।
একা হতে দিলে তো!
সারাদিন ওখানেই কাটল।
স্নান-খাওয়ার পর এবার বিশ্রামের জন্য ওই ঘরেই একটু একা হওয়ার সুযোগ পেলেন আর সময় নষ্ট না করে ঢুকে পড়লেন খাটের নীচে।
গেরস্থালির হাঁড়ি কড়াই, আরও অনেক সরঞ্জাম ঠেলে অবশেষে খাটের তলায় ওই লম্বা শরীর নিয়ে ঢুকলেন। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন খাটের নীচে নরুনের দাগ।— ‘‘ওই তো, হ্যাঁ ওই তো রয়েছে। সত্যিই রয়েছে!’’
নিজের শৈশবের করা আঁকিবুঁকিতে কয়েকবার আঙুল বুলিয়ে বেরিয়ে এলেন মানিক। গোটা শরীরে ঝুলকালি আর এক বুক আনন্দ! কিন্তু ঘরের দরজার সামনে তাকাতেই পুরো স্থির। বাড়ির সব লোক হতভম্ব হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মানিককে দেখছেন!
টাকা পাঠানো বন্ধ করলেন দাদা…
পরীক্ষায় বরাবর ভাল রেজাল্ট। কিন্তু কলেজে পড়ার সময়েই জড়িয়ে পড়লেন সক্রিয় বাম রাজনীতিতে।
তার সঙ্গে দিনরাত সাহিত্য চর্চা। কলেজের লেখাপড়া শিকেয়। ফলে বিএসসি-তে পরপর দু’বার ফেল।
তখন পড়াশোনার যাবতীয় খরচ চালাতেন বড়দা। ভাইয়ের রাজনীতি করার খবর পেয়ে চিঠিতে লিখলেন, ‘‘তোমাকে ওখানে পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়েছে, ফেল কেন করেছ, তার কৈফিয়ত দাও।’’
উত্তরে মানিক লিখলেন, গল্প উপন্যাস পড়া, লেখা এবং রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।
প্রচণ্ড রেগে গিয়ে দাদা বললেন, ‘‘তোমার সাহিত্য চর্চার জন্য খরচ পাঠানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’’ টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন দাদা।
উত্তরে মানিক লিখলেন, ‘‘আপনি দেখে নেবেন, কালে কালে লেখার মাধ্যমেই আমি বাংলার লেখকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে স্থান করে নেব। রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্রের সমপর্যায়ে আমার নাম ঘোষিত হবে।’’
ষোলো বছর বয়েসে মাকে হারানোর পর এমনিই জীবন হয়ে উঠেছিল ছন্নছাড়া, এবার দাদা টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায় শুরু হল প্রকৃত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই।
চলে এলেন আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটি মেসে। বাবা রইলেন মুঙ্গেরে ছোটভাই সুবোধের কাছে।
দিনরাত এক করে নাওয়া খাওয়া ভুলে তখন মানিক শুধু লিখছেন, প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন।
নিজের শরীরের কথা ভুলে এই ভাবে অমানুষিক পরিশ্রমের ফলও ফলল কিছু দিন পরেই।
এক সময় কুস্তি লড়া, একা হাতে দশজনের সঙ্গে মোকাবিলা করা মানিক ভেঙে যেতে থাকলেন।
১৯৩৩ সালে কলকাতায় এসেছিল এক বিখ্যাত পুতুল নাচের দল। সেই কার্নিভালের নাচ দেখে এমনই মুগ্ধ হলেন যে সেই পুতুলদের সঙ্গে মানুষের জীবনকে মিলিয়ে লিখতে শুরু করলেন ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’।
সেই উপন্যাস লিখতে বসে নিজের কথাই যেন ভুলে গেলেন মানিক।
অনেক পরে এক চিঠিতে লিখেওছেন সেই কথা। যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত মানিক’ বইয়ের ২৪ নম্বর চিঠিতে দেখতে পাই মানিক লিখছেন, ‘‘প্রথমদিকে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ প্রভৃতি কয়েকটা বই লিখতে মেতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং আমার পরিবারের মানুষরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিলেন। তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। একমাস থেকে দু’তিনমাস অন্তর এটা ঘটতে থাকে। তখন আমার বয়স ২৮/২৯, ৪/৫ বছরের প্রাণান্তকর সাহিত্যসাধনা হয়ে গেছে।’’
আক্রান্ত হলেন দূরারোগ্য মৃগীরোগে। শরীর আর দিচ্ছে না। তার মধ্যেই দাঁতে দাঁত চেপে চলছে লড়াই। নিজের রোগের সঙ্গে, চরম দারিদ্রের সঙ্গে।
এই রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই শুরু করলেন অপরিমিত মদ্যপান।
এর মধ্যেই চিকিৎসক বিধান রায়ের পরামর্শে বিয়ে করেছেন, ছেলে–মেয়ে হয়েছে। বাবাকে নিয়ে এসেছেন নিজের কাছে।
বরানগরে গোপাললাল ঠাকুর স্ট্রিটে সকলে মিলে ঠাসাঠাসি করে কোনওমতে থাকা।
তার মধ্যেই চলে একের পর এক যুগান্তকারী রচনা। এত লেখালেখি করেও সংসার যেন আর চলে না। বাধ্য হলেন চাকরি নিতে। কিন্তু কিছু দিন পরেই সে চাকরিতে ইস্তফা।
আবার পুরোদমে লেখা শুরু, সঙ্গে দারিদ্র। সে দারিদ্র যে কী ভয়ংকর তা জানা যায় মানিকের ডায়েরির একটি পৃষ্ঠা পড়লে। স্ত্রী ডলি অর্থাৎ কমলা এক মৃত সন্তানপ্রসব করেছেন, আর মানিক ডায়েরিতে লিখছেন, ‘‘বাচ্চা মরে যাওয়ায় ডলি অখুশি নয়। অনেক হাঙ্গামা থেকে বেঁচেছে। বলল, বাঁচা গেছে বাবা, আমি হিসেব করেছি বাড়ি ফিরে মাসখানেক বিশ্রাম করে রাঁধুনি বিদায় দেব। অনেক খরচ বাঁচবে।’’
দারিদ্র কী অপরিসীম হলে মায়ের মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়ে আসে!
আগে ডালভাত, পরে সাহিত্য…
সংসারের এমন অবস্থায় আবার ঠিক করলেন চাকরি করতে হবে। ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় সাপ্তাহিক বিভাগের জন্য সহকারী সম্পাদক প্রয়োজন। মানিক আবেদন করলেন।
জানতেন ওই পদের জন্যই আবেদন করবেন আরেক সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। তাই নিজের আবেদনপত্রের শেষে সম্পাদককে লিখলেন, ‘‘আমি অবগত আছি শ্রীপরিমল গোস্বামী এই পদটির জন্য আবেদন করিবেন। আমার চেয়েও তাঁহার চাকুরির প্রয়োজন বেশি। মহাশয় যদি ইতিমধ্যে তাহার সম্পর্কে অনুকূল বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক আমার এই আবেদন প্রত্যাহার করা হইল বলিয়া ধরিয়া লইবেন।’’
চাকরি অবশ্য তারই হল। মাস মাহিনা ৮৫ টাকা। সঙ্গে শর্ত ‘অমৃতস্য পুত্রা’ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। তার জন্য পাবেন আরও ১০ টাকা মাসপ্রতি। কিন্ত ভাগ্যে চাকরি নেই।
সেই চাকরিও ছেড়ে দিলেন কিছু দিন পর। অভাব ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে, তার মধ্যেই লিখে চলেছেন, বামপন্থী ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কখনও একাই প্রাণের মায়া ছেড়ে একাই ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কলকাতার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা রুখতে।
১৯৫০ সালে যখন কমিউনিস্টদের ওপর নেমে এল চূড়ান্ত সরকারি দমননীতি, তখন বহু পত্রপত্রিকায় মানিকের লেখা ছাপানো বন্ধ করে দেওয়া হল। আরও ভয়ংকর সঙ্কট।
গোটা পরিবারের হাঁ মুখের দিকে তাকিয়ে আর যেন সহ্য হত না কিছু। এক এক সময় ধিক্কার লাগত নিজের প্রতি।
মদ বাড়ছিল আর বাড়ছিল ক্ষয়। মদ ছাড়তে চেষ্টা করেও পেরে উঠছিলেন না। দাদাকে আবার চিঠি লিখলেন, কিছু টাকা ধার চেয়ে।
দাদা চিঠির উত্তরে লিখলেন, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, আমি কাউকে টাকা ধার দিই না। ভাইয়ের সঙ্গে পাবলিশিং হাউজের ব্যবসাও শুরু করলেন একবার, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে সেই ব্যবসাও মুখ থুবড়ে পড়ল।
ঘনঘন অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, হাসপাতালে ভর্তি, লিভার নষ্ট হতে থাকা মানিক পুরোপুরি বিপর্যস্ত। তার সঙ্গে চূড়ান্ত অনটন।
মনে মনে কতটা ভেঙে পড়েছিলেন মানিক তা জানতে পারা যায় একটি ছোট ঘটনায়।
একদিন ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় পুজো সংখ্যার লেখা দিতে যাচ্ছেন রাস্তায় দেখা হল অধ্যাপক বন্ধু দেবীপদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে।
মানিকের ভেঙে যাওয়া শরীর, মলিন জামাকাপড় দেখে খুব খারাপ লাগল দেবীপদর। জোর করে সে দিন নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে।
ক্লান্ত মানিককে খেতে দিলেন দেবীপদর মা। বড় তৃপ্তি করে ওই খাবারটুকু খেলেন মানিক।
তারপর যে মানিক একদিন সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন আমি শুধু সাহিত্যিকই হব, সেই মানিকই অস্ফুটে বলে উঠলেন, ‘‘দেখো, দুটি ডাল-ভাতের সংস্থান না রেখে বাংলাদেশে কেউ যেন সাহিত্য করতে না যায়।’’
জীবনে এত ফুল তিনি পাননি…
কিছু দিন আগেই হাসপাতাল থেকে জেদ করে বাড়ি ফিরেছেন। বন্ধুবান্ধবদের দেওয়া আর্থিক সাহায্য তার নিতে ইচ্ছে করে না।
কিন্তু বাধা দেওয়ার সামর্থ্যটুকুও নেই তখন। এই অবস্থার মধ্যে আবার বাড়িওয়ালা মামলা ঠুকলেন তার বিরুদ্ধে।
দিনের পর দিন ভাড়া বাকি রাখা আর তিনি সহ্য করবেন না। মানিকের কয়েকজন বন্ধু মিলে মোটা টাকার বিনিময়ে আদালতে মামলার দিন পিছিয়ে দিতে পারলেন, কিন্তু জীবনের আদালতে রায় ঘোষণার দিন এগিয়ে আসছিল। শুনতে পায়নি কেউ।
৩০ নভেম্বর, মানিক আবার জ্ঞান হারালেন।
২ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় আবার ভর্তি করা হল নীলরতন হাসপাতালে।
এমন অসুস্থতার খবর পেয়ে ছুটে এলেন কবি, কমরেড সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আর একটু পরেই অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হবে মানিককে। এবার আর বাড়ি ফেরানো যাবে ‘পদ্মানদীর মাঝি’কে? তাই নিয়ে সকলেই সংশয়ে।
সুভাষ অনুযোগ করলেন লেখকপত্নীকে, ‘‘বৌদি এমন অবস্থা, আগে টেলিফোন করেননি কেন?’’
ম্লান হেসে কমলা উত্তর দিলেন, ‘‘তাতে যে পাঁচ আনা পয়সা লাগে ভাই।’’
সেটুকুও নেই যে ঘরে!
৩ ডিসেম্বর। ভোর চারটে। পৃথিবীতে একটি নতুন দিন সবে শুরু হচ্ছে তখন, বহু দিন অনন্ত লড়াইয়ের পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল এক আটচল্লিশ বছরের জীবন।
বিকেল চারটের সময় বের হল বিশাল শোকমিছিল। নিমতলা ঘাটের দিকে এগোতে থাকল শববাহী গাড়ি।
শেষ দুই দিনের সবসময়ের সঙ্গী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিকথায় লিখছেন ‘‘পালঙ্ক শুদ্ধু ধরাধরি করে যখন ট্রাকে তোলা হয় তখন একটা চোখ খোলা, একটা বন্ধ। শরীরের ওপর রক্তপতাকা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে ফুল। মুখটুকু বাদে সমস্ত শরীরটা ফুলে আর ফুলে ছেয়ে গেছে। উপচে পড়ছে দুপাশে…। মাথা এবং পায়ের কাছে দেশনেতা এবং সাহিত্যিক! সামনে পিছনে, দুইপাশে বহু মানুষ। সর্বস্তরের মানুষ। মোড়ে মোড়ে ভিড়। সিটি কলেজের সামনে মাথার অরণ্য। কিন্তু কাল কেউ ছিল না, কিছু ছিল না…জীবনে এত ফুলও তিনি পাননি।’’
আর বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন—
ফুলগুলো সরিয়ে নাও আমার লাগছে। মালা জমে জমে পাহাড় হয় ফুল জমতে জমতে পাথর। পাথরটা সরিয়ে নাও আমার লাগছে। সেই ফুলের ভারে সেদিন সত্যিই দামি পালঙ্কের একটি পায়ায় চিড় ধরে গিয়েছিল।
————————
(লেখাটি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবং দ্য ক্যাফে টেবল প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত ‘বাংলা সাহিত্যের দশদিক’ গ্রন্থ থেকে লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা হল)







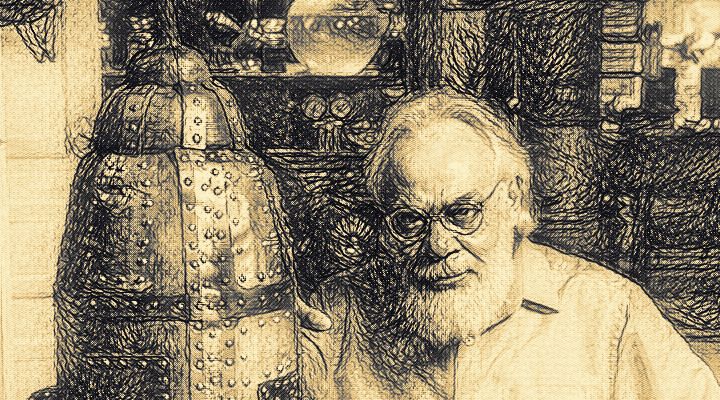
একটি অসাধারন লেখা।শেয়ার করলাম